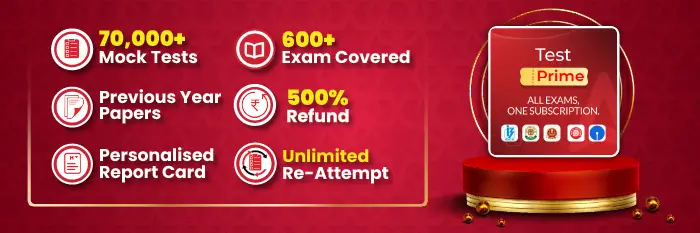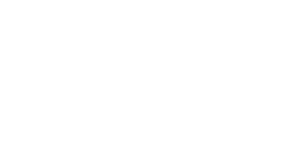Table of Contents
পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকা
পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকা বৈচিত্র্য এবং উর্বরতা সহ, রাজ্যের কৃষির মেরুদণ্ড গঠন করে। যাইহোক, মাটি ক্ষয়ের আশংকাজনক হুমকি সরকারী সংস্থা, পরিবেশবাদী, কৃষক এবং বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অবিলম্বে মনোযোগ এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার দাবি করে। টেকসই কৃষি অনুশীলন, বনায়ন, এবং উন্নত ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে, পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ মৃত্তিকা সংরক্ষণ করা কেবলমাত্র অর্জনযোগ্য নয়, এই অঞ্চলের ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। এই আর্টিকেলে, পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকা, মৃত্তিকা ক্ষয়ের কারণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকার প্রকার
ভুমিরূপ, শিলালক্ষণ, জলবায়ু, নদনদী ও উদ্ভিদের বৈচিত্রের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে নানা ধরনের মাটি সৃষ্টি হয়েছে। উৎপত্তি, গঠন, বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি ও উপাদানের ভিত্তিতে রাজ্যের মাটি পাঁচ প্রকার।
পার্বত্য অঞ্চলের মৃত্তিকা বা বাদামী পডজল মৃত্তিকা
- বন্টন : পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে শিলিগুড়ি মহকুমা বাদে সমগ্র দার্জিলিং , কালিম্পং , আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম ও কালচিনি থানা এলাকায় পার্বত্য মাটি রয়েছে। এটি পডজল মাটি নামে পরিচিত।
- উৎপত্তি : পার্বত্য ভূমির উদ্ভিদের পাতা , ফুল , লতাপাতা প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য পচে জৈব পদার্থ বা হিউমাস সৃষ্টি হয়ে মাটিতে যুক্ত হয়। অত্যাধিক বৃষ্টিপাতের ফলে উপরি স্থলের লোহা , ক্যালসিয়াম , পটাসিয়ামের খার জাতীয় পদার্থ দ্রবীভূত ও অপসারিত হয়ে নিচের স্তরে হার্ড প্যান গড়ে ওঠে। ফলে পৃষ্ঠস্তরে জৈবপদার্থ ও বালি সমৃদ্ধ ধূসর রঙের আম্লিক মাটি গড়ে ওঠে।
- বৈশিষ্ট্য : (1) এই মাটি জৈবদ্রব্য ও বালি সমৃদ্ধ অম্লধর্মী। (2) উপরিস্তরের বালির অধিক্যের জন্য ধূসর রঙের হয়। কখনো বা হালকা বাদামি রঙের হয়। (3) এটি জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ হলেও খনিজ দ্রব্য বিশেষ থাকে না। ফলে অনুর্বর। (4) খাড়া ঢাল সৃষ্টি হওয়ায় মাটির স্তর খুব পাতলা ও নুড়ি পাথরে পূর্ন। (5) মাটির ধৌতক্ষয় ও ধস প্রবণতা অনেক বেশি।
- গুরুত্ব : উর্বরতা শক্তি কম হলেও চা, কমলালেবু, সিঙ্কোনা, বিভিন্ন মশলা, ফলমূল, তামাক, ভুট্টা, আলু চাষ হয়।
ধূসর-বাদামি জাতীয় মৃত্তিকা বা তরাই অঞ্চলের মৃত্তিকা
- বন্টন : পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলে দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা এবং আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির উত্তরাংশে এই মাটি রয়েছে। একে তরাই মাটিও বলে।
- উৎপত্তি : তরাই অঞ্চলের পর্ণমচি অরণ্যের ঝরা পাতা , ফুল উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের হ্রাস বৃদ্ধির জন্য স্বল্প হিউমাস সৃষ্টি হয় এবং ধৌত প্রক্রিয়ার অভাবে সিলিকা খনিজ মাটির উপরিস্তরে থেকে গাঢ় ধূসর ও বাদামি রঙের পডজল জাতীয় মাটি সৃষ্টি হয়।
- বৈশিষ্ট্য : (1) এই মাটি অপেক্ষাকৃত কম আম্লিক। (2) উপরিস্তরে সিলিকেট খনিজ ও লোহা অক্সাইডের জন্য গাঢ় ধূসর ও বাদামি রঙের হয়। (3) এতে জৈবপদার্থের সঙ্গে বিভিন্ন খনিজ মিশ্রিত থাকায় পডজল অপেক্ষা উর্বর হয়। (4) এই মাটি বালি, কাঁকর ও পলি মিশ্রিত বেলে দোআঁশ প্রকৃতির এবং জলধারণ ক্ষমতা কম। (5) গভীর বনভূমির জন্য মাটিতে জৈব পদার্থ বেশি থাকে।
- গুরুত্ব : উর্বরতা বেশি হওয়ায় এই মাটিতে চা, ধান, গম, আলু, কমলালেবু, আনারস, জোয়ার চাষ হয়।
মালভূমি অঞ্চলের বাদামী ও লালচে রঙের ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা
- বন্টন : ল্যাটিন শব্দ ‘ল্যাটার’-এর অর্থ ইট। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে মালভূমি অঞ্চলে 15০ মিটার সমোন্নতি রেখার উপরে সমগ্র পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম জেলার পশ্চিমাংশে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মালভূমি অঞ্চলে এবং দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহ জেলার বরেন্দ্রভূমি অঞ্চলে এই মাটি দেখা যায়।
- উৎপত্তি : বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে ধৌত প্রক্রিয়ায় পৃষ্টস্তরের বালি, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, সোডিয়ামের ক্ষারীয় দ্রবণীয় পদর্থগুলি নিচের স্তরে অপসৃত হয়। পৃষ্টস্তরে অদ্রবণীয় লোহা ও আলুমিনিয়াম অক্সাইড ও হাইড্রোঅক্সাইড শুস্ক ঋতুতে জমাটবদ্ধ হয়ে লাল রঙের ইটের মতো শক্ত ল্যাটেরাইট সৃষ্টি হয়।
- বৈশিষ্ট্য : (1) পৃষ্ঠ স্তর থেকে ক্ষারীয় অক্সাইড গুলি নিম্নস্তরে স্থানান্তরিত হওয়ায় মাটি অম্লধর্মী হয়। (2) অধিক উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের জন্য জীবদেহাবশেষ দ্রুত পচে অপসারিত হওয়ায় মাটি জৈব পদার্থহীন অনুর্বর হয়। পটাস ও ফসফরাস কম থাকে। (3) লোহা ও আলুমিনিয়াম অক্সাইডের আধিক্যেকর জন্য মাটি লাল, বাদামি ও হলদে রঙের হয়। (4) সেসক্যুই অক্সাইডের জন্য মাটি ইটের মতো খুবই শক্ত। কাঁকরের মতো বড়ো দলা যুক্ত। মোরাম সৃষ্টি হয়। মৌচাকের মতো গর্ত সমন্বিত হয়। ফলে জলধারণ ক্ষমতা কম হয়। (5) আদ্র অবস্থায় নরম হলেও শুকিয়ে গেলে শক্ত ইটের মতো হয়।
- গুরুত্ব : কাঁকুড়ে, জলধারণ ক্ষমতা কম ও জৈবপদার্থহীন হওয়ায় এটি কৃষির অনুপযুক্ত। জলসেচের সাহায্যে কিছু পরিমানে ধান, সরষে, বাদাম, গম, ভুট্টা চাষ হয়। গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট ও বাড়িঘর নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।
সমভূমি অঞ্চলের উর্বর পলিমৃত্তিকা
বন্টন : জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় এই মাটি দেখতে পাওয়া যায়।
বৈশিষ্ট্য : (1) এই মাটির গভীরতা খুব বেশি। (2) মাটি কিছুটা আম্লিক প্রকৃতির। (3) মাটিতে বালি ও পলির পরিমাণ বেশি থাকে। (4) এই মাটি অত্যন্ত উর্বর প্রকৃতির। চাষের জন্য খুব উপযোগী। (5) গঠন, উৎপত্তি ও অবস্থানের তারতম্যের ভিত্তিতে এই মাটিকে দুইভাগে ভাগ করা হয় – প্রাচীন পলিমাটি ও নবীন পলিমাটি। (6) প্রাচীন পলিমাটির রং লালচে বা হালকা লাল এবং নবীন পলিমাটি প্রধানত ধূসর বাদামী রঙের। (7) প্রাচীন পলিমাটির তুলনায় নবীন পলিমাটি বেশি উর্বর হয়।
- প্রাচীন লালচে পলিমাটি :- ল্যাটেরাইট মৃত্তিকাতে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য পলিমাটি অনেকটা লালচে রঙের হয়। সূক্ষ্ম বালির সঙ্গে পলির সংমিশ্রণের জন্য এই মাটির জলধারণ ক্ষমতা আছে। তাই জলসেচের ব্যবস্থা ছাড়াই এই মাটিতে চাষবাস হয়। বীরভূম জেলার উত্তরপ্রান্তে এবং দক্ষিন দিনাজপুর ও মালদহ জেলার পূর্বপ্রান্তে এই প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়।
- নবীন বাদামী পলিমাটি :- নদী ও সমুদ্রবাহিত পলি থেকে এই প্রকার মাটির সৃষ্টি হয়। এই মাটিতে বালি ও কাদার ভাগ সমান থাকে। পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় সমভূমি ও নদী উপত্যকার বিস্তৃত অঞ্চলগুলিতে যেমন – মালদহ, মুর্শিদাবাদের কিছু অংশ, নদীয়া, হুগলী, হাওড়া, উঃ ও দঃ 24 পরগণা, মেদিনীপুর জেলার পূর্বাংশ, কোচবিহার ও দিনাজপুরের কিছু অংশে দেখা যায়। এই মাটি অত্যন্ত উর্বর প্রকৃতির। এই মাটিতে প্রচুর ধান, গম, পাট, তৈলবীজ প্রভৃতির চাষ হয়। এই অঞ্চলকেই প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যভান্ডার বলা হয়।
গুরুত্ব : এই মাটি অত্যন্ত উর্বর প্রকৃতির ও চাষের জন্য খুব উপযোগী হওয়ায় ধান, গম, পাট, আখ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে এই পলিমাটিতে উৎপাদিত হয়।
উপকূলের লবনাক্ত মৃত্তিকা
বন্টন : সুন্দরবন ও কাঁথি সংলগ্ন উপকূল অঞ্চলে প্রধানত এই মাটি দেখতে পাওয়া যায়।
বৈশিষ্ট্য : (1) এই মাটির গভীরতা খুব বেশি। (2) মাটির কণাগুলি খুব সূক্ষ্ম হয়। (3) মাটিতে লবণের পরিমাণ খুব বেশি থাকে। (4) এই মাটিতে জোয়ার ভাটার প্রভাব বেশি বলে মাটি আদ্র ও লবণাক্ত প্রকৃতির হয়। (5) এই মাটির রং কালচে প্রকৃতির হয়। (6) মাটি মূলত অনুর্বর প্রকৃতির হয়।
গুরুত্ব : বৃষ্টির জলের মাধ্যমে বিশেষ পদ্ধতিতে মাটির লবণতা হ্রাস করে নারকেল, সুপারি, ধান, তরমুজ, লঙ্কা, শাকসবজি প্রভৃতি উৎপাদন করা হয়।
পশ্চিমবঙ্গে মৃত্তিকা ক্ষয়ের কারণ
মৃত্তিকা ক্ষয় পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ও মানবীয় কার্যাবলীর দ্বারা মৃত্তিকার উপরিভাগ যখন অত্যন্ত ধীরগতিতে বা দ্রুতগতিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন তাকে সাধারণভাবে মৃত্তিকা ক্ষয় বলে। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে মৃত্তিকার উপরিভাগ ধীরগতিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মানুষের বিভিন্ন কার্যাবলীর দ্বারা মৃত্তিকা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। পশ্চিমবঙ্গে মৃত্তিকা ক্ষয় সাধারণত দুইভাবে হয়ে থাকে। যথা (ক) প্রাকৃতিক কারণে ভূমিক্ষয় (খ) মানবিক কারণে ভূমিক্ষয়।
প্রাকৃতিক কারণ:-
জলপ্রবাহ : জলপ্রবাহ মৃত্তিকা ক্ষয় কারী প্রাকৃতিক শক্তি গুলির মধ্যে অন্যতম। বৃষ্টিপাত অপেক্ষা অনুপ্রবেশ কম হলে জলপ্রবাহের দ্বারা মৃত্তিকা ক্ষয় প্রাধান্য লাভ করে। জলপ্রবাহ প্রধানত Sheet erosion, Gully erosion, Rill Erosion – এই তিনটি পদ্ধতিতে মৃত্তিকার ক্ষয় সাধন করে।
বৃষ্টিপাত : বৃষ্টিপাত যে কেবলমাত্র জলপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই নয়, মৃত্তিকা ক্ষয়েও সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। বৃষ্টির ফোঁটা মৃত্তিকার ওপর আঘাত করে তার দ্বারা দানাকৃতি গঠনকে ভেঙে মৃত্তিকার কণাগুলিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মৃত্তিকার এই বিচ্ছিন্ন কণাগুলি জল স্রোতে ভেসে যায়। ফলে মৃত্তিকা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এছাড়া বৃষ্টিপাতের ফলে মাটি সিক্ত হয় বলে মৃত্তিকার কণাগুলি সহজে শিথিল ও জলে দ্রবীভূত হয়ে অপসারিত হয়। ফলে মৃত্তিকা ক্ষয় ঘটে।
বায়ুর কার্য : সাধারণত গাছপালা হীন মৃদু ঢাল যুক্ত শুষ্ক ভূমি ভাগে মৃত্তিকা স্তর আলগা হওয়ায় বায়ুপ্রবাহ দ্বারা মৃত্তিকা ক্ষয় সর্বাধিক হয়। প্রবল বায়ু প্রবাহের দ্বারা শিথিল মৃত্তিকা কণা একস্থান থেকে অন্যস্থানে পরিবাহিত হওয়ার ফলে মৃত্তিকা ক্ষয় ঘটে। বায়ুর এই ক্ষয়কারী ক্ষমতা নির্ভর করে বায়ুর গতিবেগ, উদ্ভিদ বিরল অঞ্চল ও বায়ুবাহিত কোয়ার্টাজ কণার পরিমাণের ওপর।
ভূমির ঢাল : ভূমির ঢালের মাত্রার ওপর জলপ্রবাহের দ্বারা মৃত্তিকা ক্ষয় বিশেষভাবে নির্ভরশীল। ঢাল বিহীন বা মৃদু সমতলভূমিতে মৃত্তিকা ক্ষয়ের পরিমাণ কম। কিন্তু অধিক ঢাল যুক্ত ভূমিতে উদ্ভিদের আবরণ না থাকলে ভূমিক্ষয় খুব বেশি হয়।
ভূমিধস : উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে বা খাড়াই পাহাড়ি ঢালে ভূমিধসের ফলে প্রচুর পরিমাণে মৃত্তিকা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। উত্তরপ্রদেশের গাড়োয়াল হিমালয় অঞ্চলে ভূমিধসের ফলে প্রতিবছর প্রায় 5০০ মেট্রিক টন মৃত্তিকা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।
ঝড় ও বন্যা : ঝড়ের সময় মৃত্তিকার শিথিল কণাগুলি একস্থান থেকে অন্য স্থানে অপসারিত হয় বলে মৃত্তিকা ক্ষয় ঘটে। আবার বন্যার সময় জলের তীব্র স্রোতেও যথেষ্ট পরিমাণে মৃত্তিকা ক্ষয় হয়ে থাকে।
মানবীয় কারণ :-
অনিয়ন্ত্রিত বৃক্ষ ছেদন : উদ্ভিদের শেকড় একদিকে যেমন মৃত্তিকাকে শক্তভাবে ধরে রাখতে সাহায্য করে, অন্যদিকে তেমনি জল ও বায়ু প্রবাহের গতিবেগকে প্রতিহত করেও তাদের ক্ষয়কারী ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু মানুষ কৃষি, শিল্প, রাস্তাঘাট ও বাসস্থানের ভূমি সংস্থানের প্রয়োজনে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃক্ষছেদন করার ফলে মৃত্তিকা স্তর শিথিল হয়ে মৃত্তিকা ক্ষয় ত্বরান্বিত হয়।
অবৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকাজ : আদিম জনগোষ্ঠীর লোকেরা পাহাড়ি ঢালে বনভূমি পুড়িয়ে মৃত্তিকা খনন করে কৃষি কাজ করে। এক অঞ্চলের মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাস পেলে তারা অন্যত্র গমন করে এবং সেখানেও একই পদ্ধতিতে কৃষি কাজ করে। ফলে পূর্বের পরিত্যক্ত জমির আলগা মৃত্তিকা স্তর সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।
অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণ : তৃণ মৃত্তিকার ওপর আচ্ছাদনের আকারে অবস্থান করে জলের পৃষ্ঠ প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে। এছাড়া তৃণের শেকড় মৃত্তিকাকে শক্তভাবে ধরে রাখে। কিন্তু তৃণভূমি অঞ্চলে অনিয়ন্ত্রিতভাবে পশুচারণ ক্ষেত্র গড়ে উঠলে ওই তৃণ দ্রুত অবলুপ্ত হয় এবং মৃত্তিকা স্তর উন্মুক্ত ও আলগা হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহের দ্বারা ওই উন্মুক্ত স্তরের আলগা মৃত্তিকা কণা সমূহ অন্যত্র অপসারিত হয়। ফলে মৃত্তিকা ক্ষয় ঘটে।
নির্মাণকার্য : মানুষ কৃষির প্রয়োজনে জলাধার ও বাঁধ নির্মাণ করে, ভূমি কর্ষণ করে কৃষি ক্ষেত্র তৈরি করে, যাতায়াতের প্রয়োজনে রাস্তাঘাট নির্মাণ করে এবং বসতির প্রয়োজনে গৃহ নির্মাণ করে। এইসব নির্মাণকাজের প্রভাবে মৃত্তিকার উপরিস্তর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা ওই দুর্বল মৃত্তিকা স্তর অন্যত্র অপসারিত হয়। ফলে মৃত্তিকা ক্ষয় ঘটে।
মৃত্তিকা সংরক্ষণের পদ্ধতি
পরিবেশবিদগণ মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ করার জন্য বেশ কিছু উপায় বা পদ্ধতির কথা বলেছেন। মৃত্তিকা সংরক্ষণের সেই উপায় বা পদ্ধতিগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। যথা –
মৃত্তিকা সংরক্ষণের কৃষি অনুসৃত পদ্ধতি
নিয়ন্ত্রিত হারে বৃক্ষচ্ছেদন ও নতুন বনসৃজন : মৃত্তিকা সংরক্ষণের একটি প্রধান উপায় হল নিয়ন্ত্রিত হারে বৃক্ষছেদন ও নতুন বনসৃজন। অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃক্ষছেদন করলে মৃত্তিকা দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলে একমাত্র প্রয়োজন অনুযায়ী পরিণত বৃক্ষ ছেদন করে অপরিণত বৃক্ষগুলি রক্ষার দ্বারা মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ করা যায়। এছাড়া অনুর্বর ও পতিত জমিতে এবং পাহাড়ের ঢালে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ করে নতুন বনসৃজনের দ্বারা মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ করা সম্ভব। কারণ বৃক্ষের শেকড় মৃত্তিকার কণাগুলিকে দৃঢ় ভাবে পরস্পরের সাথে আটকে রাখে এবং একই সাথে জল ও বায়ু প্রবাহের প্রভাব জনিত ক্ষয়ের হাত থেকে মৃত্তিকাকে রক্ষা করে।
নিয়ন্ত্রিত পশুচারণ : তৃণ মৃত্তিকার ওপরে আচ্ছাদনের আকারে অবস্থান করে এবং তৃণের শেকড় মৃত্তিকাকে শক্তভাবে ধরে রেখে মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ করে। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিতভাবে পশুচারণের ফলে মৃত্তিকার উপরিভাগের তৃণস্তর বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই নিয়ন্ত্রিতভাবে পশুচারণ করলে তৃণ বা ঘাসের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে এবং মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয়।
শস্যাবর্তন পদ্ধতি অনুসরণ : একই জমিতে একই ফসল বার বার চাষ করলে মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাস পায় এবং মৃত্তিকা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু একই জমিতে সুযোগ-সুবিধা মত যদি দুই বা ততোধিক ফসল পর্যায়ক্রমে চাষ করা যায় বা শস্যাবর্তন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তাহলে জমির স্বাভাবিক উর্বরতা শক্তি বজায় থাকে এবং মৃত্তিকার রাসায়নিক উপাদানগুলির ক্ষয় নিয়ন্ত্রিত হয়।
নিয়ন্ত্রিত স্থানান্তর কৃষি পদ্ধতি : স্থানান্তর কৃষি পদ্ধতিতে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে বনাঞ্চল ধ্বংস করে ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভূমিকর্ষণের দ্বারা কৃষি কাজ করার ফলে মৃত্তিকা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তাই স্থানান্তর কৃষির (ঝুম চাষের) ব্যাপকতা নিয়ন্ত্রণ করে মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ করা সম্ভব।
ধাপ চাষ পদ্ধতি অনুসরণ : উচ্চ ঢাল যুক্ত পাহাড়ি অঞ্চলে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি কাজ করলে মৃত্তিকা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তাই উচ্চ ঢাল যুক্ত পাহাড়ি অঞ্চলে সমোন্নতি রেখার সমান্তরালে জমির ওপর ধাপ কেটে কৃষিকাজ করলে মৃত্তিকার উপরের স্তরটি সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হতে পারে না। ফলে মৃত্তিকা ক্ষয় কম হয়।
জৈব উপাদানের সংরক্ষণ : মৃত্তিকার ওপর সঞ্চিত জৈব পদার্থ তথা পাতা, ডালপালা, খড় ইত্যাদি মৃত্তিকাকে বৃষ্টিপাতের আঘাতজনিত ক্ষয় থেকে রক্ষা করে। এছাড়া ওইসব জৈব পদার্থ হিউমাসে পরিণত হয়ে মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি করে।তাই ওইসব জৈব পদার্থ সংরক্ষণের দ্বারা মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ করা সম্ভব।
উপরিলিখিত জৈবিক পদ্ধতি গুলি ছাড়াও সমোন্নতি কৃষি, বলয় কৃষি, নতুন তৃণভূমি সৃষ্টি, নতুন অরণ্য বলয় সৃষ্টি ইত্যাদি জৈবিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমেও মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ করা যায়।
মৃত্তিকা সংরক্ষণের কারিগরি পদ্ধতি
কৃত্রিম দেওয়াল নির্মাণ : মৃত্তিকার জলনালিকা ক্ষয় রোধ করার জন্য গভীর নালির সঙ্গে আড়াআড়িভাবে পাথর ও কংক্রিটের কৃত্রিম দেওয়াল নির্মাণ করে এবং মাটি দিয়ে নালিগুলি ভরাট করে মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ করা যায়।
মৃত্তিকার জল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি : কৃত্রিম উপায়ে মৃত্তিকার জল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে মৃত্তিকার ওপর জলের ক্ষয়কারী শক্তির তীব্রতা কমিয়ে মৃত্তিকার ক্ষয় রোধ করা যায়।
বায়ু প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ : শুষ্ক অঞ্চলে মৃত্তিকা ক্ষয়ের প্রধান কারণ হলো বায়ুপ্রবাহ। উক্ত অঞ্চলে মৃত্তিকাকে আর্দ্র রেখে বায়ুর গতিপথে আড়াআড়িভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে অথবা মৃত্তিকাকে জৈব পদার্থে আবৃত করে বায়ু প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ করা সম্ভব।
অন্যান্য উপায় : উপরিলিখিত পদ্ধতিগুলি ছাড়াও নিচু জমিতে বন্যা রোধ করার জন্য বাঁধ নির্মাণ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বৃক্ষছেদন ও নতুন বৃক্ষরোপণ, ভূমিক্ষয় প্রতিরোধে ব্যাপক প্রচার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমেও মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ করা যায়।